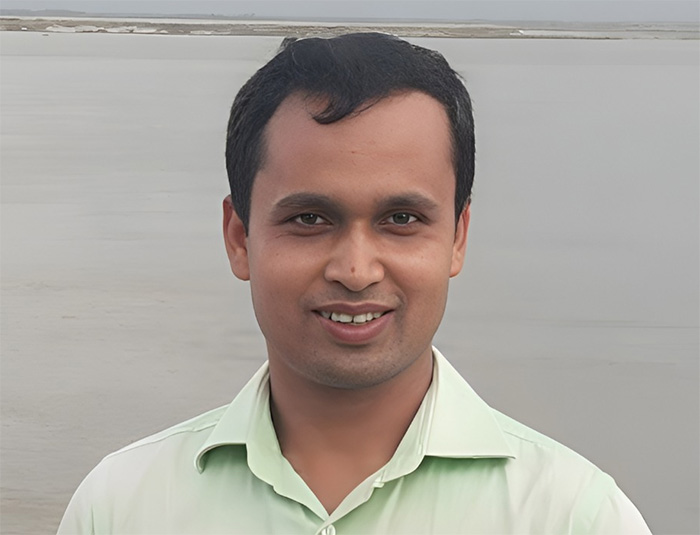.jpg)
নয়া বাজেট আসন্ন। আগামী ২ জুন উপস্থাপিত হতে পারে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট। এখন বাজেট প্রণয়নের কাজ চলছে। এরই মধ্যে জানা গেছে, আগামী বাজেটের আকার হতে পারে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরের মূল বাজেটের তুলনায় তা হবে ৭ হাজার কোটি টাকা কম। স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম টাকার অংকে বাজেটের আকার হ্রাস পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ বাজেট হবে সংকোচনমূলক। চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব আহরণের ধীরগতি ও বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতার অভাবহেতু একটি আঁটসাঁট বাজেটই আমাদের কাম্য।
বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এর চেয়েও রক্ষণশীল ও ছোট অংকের একটি বাজেট বেশি উপযোগী হতে পারে। এর লক্ষ্য হতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, নিম্ন আয়ের মানুষের কষ্ট লাঘব ও দুর্বৃত্তায়নের লাগাম টেনে ধরা। উৎপাদনশীল কৃষি খাত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্ব দিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতের খরচ হ্রাস করা এখন খুবই প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি বাজেটের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এখন আমাদের প্রয়োজন ব্যয় কমিয়ে এবং খরচের গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি বাস্তবসম্মত বাজেট অনুসরণ করা।
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান নির্দেশক হচ্ছে দেশজ আয়ের প্রবৃদ্ধির হার। প্রতিটি বাজেটেই এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। চলতি অর্থবছর (২০২৪-২৫) জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। পরে তা পুনর্নির্ধারণ করা হয় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এখন তা আরো হ্রাস করে নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। তবে উন্নয়ন-সহযোগী সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস হচ্ছে অনেক কম। বিশ্বব্যাংক যে পূর্বাভাস দিচ্ছে তাতে এ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। আইএমএফের পূর্বাভাস হলো ৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলছে, প্রবৃদ্ধির হার হতে পারে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।
এবার জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম অনুমিত হওয়ার কারণ হলো সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিনিয়োগ হ্রাস ও উৎপাদনে স্থবিরতা। অর্থবছরের শুরুতে খরা, পরে ভয়াবহ বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে কৃষির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। মানুষের আয় কমে যায়। আগামী বছর প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রধান নিয়ামক হবে সুস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫ থেকে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।
প্রবৃদ্ধির হার মাঝারি গোছের হলেও জনজীবনে স্বস্তি থাকতে পারে, যদি তা উচ্চ মূল্যস্ফীতির অতলে তলিয়ে না যায়। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দুষ্ট ক্ষত হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি, যা গরিব ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষদের চরমভাবে ভোগান্তিতে ফেলে। জনজীবনে কষ্ট ও দুর্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে প্রায় তিন বছর ধরে বিরাজ করছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এর মাত্রা গড়ে ৯-১০ শতাংশের ওপরে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল গড়ে ৯ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। এবার গত জুলাইয়ে ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, নভেম্বরে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ, ডিসেম্বরে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশ ও এপ্রিলে ৯ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।
মূল্যস্ফীতির হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে তিন মাস ধরে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রণীত বাজেটে মূল্যস্ফীতির হার প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। গত ১০ মাসের গড় অর্জন প্রায় ১০ শতাংশ। আইএমএফের পূর্বাভাস হলো ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি, যা নিরীহ ও গরিব মানুষের কষ্ট অনেক বাড়িয়েছে।
খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার গত জুলাইয়ে ছিল ১৪ দশমিক ১০ শতাংশ, নভেম্বরে ছিল ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ। পরে তা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে এপ্রিলে নেমে আসে ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশে। এবার ডিসেম্বর পর্যন্ত উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ ছিল বন্যা ও অতিবৃষ্টিজনিত ব্যাপক শস্যহানি। পরে রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শাকসবজিসহ আলু ও পেঁয়াজের ব্যাপক মূল্যহ্রাসের কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পায়।
তবে এখন পর্যন্ত আমাদের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়ে ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার আমাদের চেয়ে প্রায় অর্ধেক কম। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক খাদ্যনিরাপত্তা ও মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে ঝুঁকির লাল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির জন্য আশঙ্কা করা হচ্ছে এ বছর দারিদ্র্যের হার ২৩ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। নিম্ন দারিদ্র্যে আরো প্রায় ৩০ লাখ নতুন মুখ যুক্ত হবে।
নতুন অর্থবছর ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে এ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে অনুসৃত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সঙ্গে সুস্থির রাজনীতির সমন্বয় করে এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের মতো মাথাপিছু কম আয়ের একটি দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৪ শতাংশের নিচে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২-৩ শতাংশে নামিয়ে আনা উচিত।
খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রধান শর্ত হলো কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি। সম্প্রতি কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এর প্রবৃদ্ধির হার এগিয়ে চলছে অনেক ধীর গতিতে। এখন কৃষি খাতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি খুবই কম। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ৫৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ৩ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছে। সার্বিক কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ২১ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্জিত ৬ দশমিক ৫৫ শতাংশের অর্ধেক মাত্র। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষি খাতের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ৪-৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।
এজন্য কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। ২০১১-১২ অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৪ দশমিক ৭৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে তুলনায় কৃষি বাজেট বাড়েনি। এ সময় কৃষি বাজেট বেড়েছে ৩ দশমিক ৭৮ গুণ। ২০১১-১২ অর্থবছরের মোট বাজেটে কৃষি বাজেটের হিস্যা ছিল ১০ দশমিক ৬৫ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তা নেমে আসে ৫ দশমিক ৯৪ শতাংশে। একইভাবে কৃষি ভর্তুকির হিস্যা নেমে আসে ৬ দশমিক ৪ থেকে ২ দশমিক ১৬ শতাংশে। অর্থাৎ যে হারে মোট বাজেট বেড়েছে সে হারে কৃষি বাজেট ও ভর্তুকি বাড়েনি।
চলতি অর্থবছরে কৃষিবিষয়ক পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৪৭ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে শস্য কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৭ হাজার ২৪১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। অন্যদিকে ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বন ও পরিবেশ, ভূমি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটা ছিল অপ্রতুল। ফসল কৃষি খাতের বরাদ্দে আগের বছরের সংশোধিত বরাদ্দ থেকে ১৮ দশমিক ২১ শতাংশ কমিয়ে দেয়া হয়েছিল।
২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তা কমিয়ে রাখা হয় ১৭ হাজার ২৬১ কোটি টাকা। এবার বন্যার কারণে আউশ ও আমন ধানের উৎপাদন মার খেয়েছে। চালের উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে চালের দাম। বেড়েছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি। বর্তমানে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে তা হ্রাস পাচ্ছে। এ ধারাকে গতিশীল করার জন্য কৃষিতে বরাদ্দ ও ভর্তুকি বাড়ানো দরকার।
উপকরণ ভর্তুকির সঙ্গে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ওপর মূল্য সহায়তা দেয়া দরকার। গত তিন-চার মাস বাজারে শাকসবজি, আলু ও পেঁয়াজের দাম অপেক্ষাকৃত কম। তাতে স্বস্তিতে আছেন ভোক্তারা। কিন্তু খুবই অস্বস্তিতে আছেন কৃষক। খামারপ্রান্তে পণ্য বিক্রি করে অনেক ক্ষেত্রে তারা উৎপাদন খরচটুকুও তুলতে পারছেন না। এমতবস্থায় মূল্য সহায়তা স্কিম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে কৃষকরা লোকসান থেকে পরিত্রাণ পাবেন। আগামী বাজেটে তার বিধান থাকা উচিত। মোট বাজেটে কৃষি খাতের হিস্যা বাড়ানো উচিত। বৃহত্তর কৃষি খাতে মোট বাজেটের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ বরাদ্দ এবং ৫ শতাংশ ভর্তুকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
বাজেট প্রণয়নের সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি কত হবে তা বলা হয় না। অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি খাতে ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৪ শতাংশ। অর্জিত হয়েছে ৩ দশমিক ২ শতাংশ। এ হার বাড়ানো দরকার। ন্যূনপক্ষে তা ৪ শতাংশ অর্জন করা উচিত। অন্যথায় মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
বর্তমানে কৃষিতে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষি জিডিপিতে শস্য খাতের শরিকানা ছিল ৭৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। প্রাণী, মৎস্য ও বনজ সম্পদের শরিকানা ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৬৬, ১০ দশমিক ৪৮ ও ৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের ফলে শস্য খাতের শরিকানা কমে গিয়ে ৪৬ দশমিক ৭৫ শতাংশে দাঁড়ায়। প্রাণী, মৎস্য ও বনজ সম্পদের শরিকানা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৬ দশমিক ৩৭, ২১ দশমিক ৫৮ ও ১৫ দশমিক ৩০ শতাংশে উপনীত হয়।
দেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ঘটছে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। তাই দুধ, ডিম, মাংস ও মাছ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা দরকার। আগামী বাজেটেও তার প্রতিফলন থাকা উচিত। উপখাতওয়ারি বরাদ্দ ও ভর্তুকির নীতিমালায় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়।
বর্তমানে দেশে পশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এদের উৎপাদিত বস্তু দুধ, মাংস ও ডিমের মূল্য অনেক চড়া। ক্ষেত্রবিশেষে তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। এর প্রধান কারণ উৎপাদনের উপকরণ খরচ বেশি। বিশেষ করে পশুখাদ্যের মূল্য খুবই চড়া। এর দাম কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা উচিত। মাছের ক্ষেত্রে সম্প্রতি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না।
প্রতি বছর প্রায় ১ শতাংশ হারে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো দখল হয়ে যাচ্ছে বা দূষণে হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। নদীনালায় মাছ ধরার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান থাকায় পোনা মাছ পর্যন্ত ধরে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ। এ সুযোগ সীমিত হওয়া উচিত। সমুদ্রের বিশাল ভাণ্ডার থেকে মৎস্য আহরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। বর্তমানে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ খুবই কম।
কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে আমাদের সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এখানে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। মৌসুমি ফল, শাকসবজি ও পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। ধান-চাল সংরক্ষণের জন্য ন্যূনপক্ষে ৪০ লাখ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম নির্মাণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে চালু থাকা গুদামগুলোর ধারণক্ষমতা মাত্র ২২ লাখ টন। এগুলো কৃষি বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। কৃষিপণ্যের রফতানি উৎসাহিত করার জন্য একসময় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হতো। বর্তমানে তা ১০ শতাংশের বেশি নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তা বাড়ানো যেতে পারে।
কৃষিকাজে এখনো যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত। সে কারণে প্রতি ইউনিট পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদন খরচ হ্রাস ও পণ্যের মান বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। দুই বছর ধরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎসাহিত করার জন্য ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন ওই প্রকল্প অকার্যকর। বিগত সরকারের আমলে দুর্বৃত্তায়নের কারণে এটি বন্ধ করা হয়। বর্তমানে তা নতুন আঙ্গিকে শততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে চালু করা যেতে পারে।
বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব খুবই বেশি। এর মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকা উচিত। কয়েক বছর ধরে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষির উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। তাতে দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকরা। তাদের সহায়তার জন্য দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল গঠন করা দরকার। আসন্ন বাজেটটি কৃষি ও কৃষকবান্ধব হবে এটাই প্রত্যাশা।
- ড. জাহাঙ্গীর আলম: একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিবিদ; সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ